আজকের আলোচনার বিষয়ঃ জ্যামিতিক কোণ ও ত্রিকোণমিতিক কোণ। যা উচ্চতর গণিতের ত্রিকোণমিতি অংশের অন্তর্গত।
ত্রিকোণমিতি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ‘ত্রিকোণ এবং মিতি বলতে পরিমাপ বুঝায়। ইংরেজিতে ত্রিকোণা বিশ্লেষণেও পাওয়া যায় ‘Trigon’ এবং ‘Metry’। ‘Trig এবং ‘Metry’ দ্বারা পরিমাপ বুঝায়। সাধারণভাবে ত্রিকো ব্যবহারিক প্রয়োজনে ত্রিভুজের তিনটি কোণ ও তিনটি বিষয়ের আলোচনা থেকেই ত্রিকোণমিতির সূত্রপাত হয়।
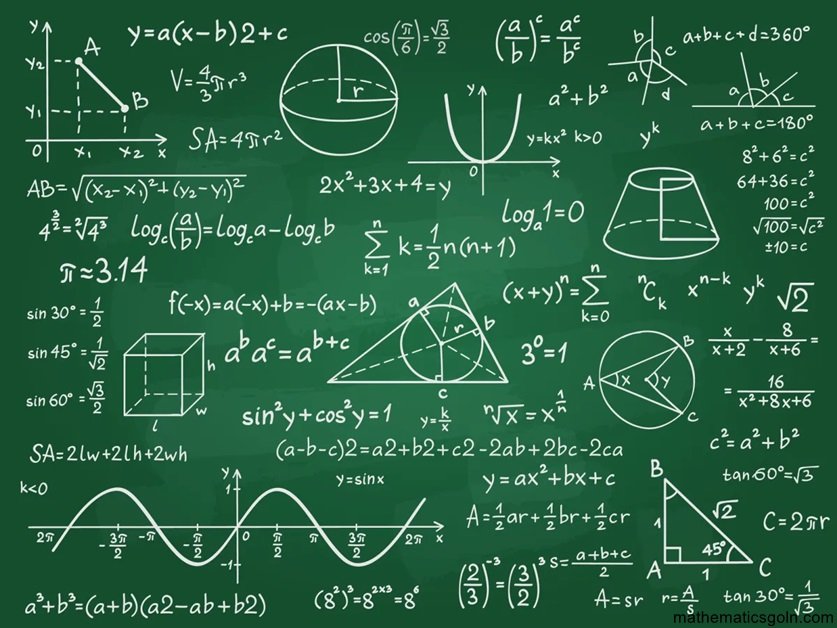
জ্যামিতিক কোণ ও ত্রিকোণমিতিক কোণ
জ্যামিতিক কোণ এবং ত্রিকোণমিতিক কোণের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা XY সমতলে পরস্পর সমকোণে ছেদ করে এরূপ একজোড়া সরলরেখা XOX’ এবং YOY’ অঙ্কন করি। নিচের চিত্রে রেখাদ্বয় O বিন্দুতে ছেদ করায় যে চারটি সমকোণ উৎপন্ন হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির অভ্যন্তরকে একটি চতুর্ভাগ (Quadrant) বলা হয়। OX রেখা থেকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকলে প্রথম সমকোণের (∠XOY এক সমকোণ) অভ্যন্তরকে প্রথম চতুর্ভাগ (First quadrant) এবং একইভাবে ঘুরতে থাকলে দ্বিতীয় (∠YOX’), তৃতীয় (∠X’OY’) এবং চতুর্থ (∠XOY’) সমকোণের অভ্যন্তরসমূহকে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চতুর্ভাগ বলা হয় (নিচের চিত্র)।

জ্যামিতিক ধারণা অনুসারে দুইটি ভিন্ন রশ্মি একটি বিন্দুতে মিলিত হলে ঐ বিন্দুতে একটি কোণ উৎপন্ন হয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে একটি স্থির রশ্মির সাপেক্ষে অপর একটি ঘূর্ণায়মান রশ্মির বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন কোণ বিবেচনা করা হয়। মনে করি, OA একটি ঘূর্ণায়মান রশ্মি এবং এটি শুরুতে OX স্থির রশ্মির অবস্থান থেকে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘুরে তার বিপরীত (anticlockwise) দিকে ঘুরছে।
OA রশ্মি প্রথমে OA অবস্থানে এসে ∠XOA, সূক্ষ্মকোণ উৎপন্ন করে এবং প্রথম চতুর্ভাগে থাকে এবং পরে যখন OX এর সাথে লম্বভাবে OY অবস্থানে আসে তখন ∠XOY কোণের পরিমাপ 90° বা এক সমকোণ হয়। OA রশ্মিটি একই দিকে আরও কিছু ঘুরে যখন OA, অবস্থানে আসে তখন ∠XOA2 কোণটি স্থূলকোণ। একইভাবে ঘুরে যখন OA রশ্মি OX এর ঠিক বিপরীত দিকে OX’ অবস্থানে থাকে, তখন উৎপন্ন কোণ ∠XOX’ একটি সরলকোণ বা দুই সমকোণ। OA রশ্মি যখন সম্পূর্ণরূপে ঘুরে ঠিক আগের অবস্থানে আসে অর্থাৎ OX এর সাথে মিলিত হয় তখন মোট উৎপন্ন কোণের পরিমাণ দুই সরলকোণ বা চার সমকোণ হয়।
জ্যামিতিতে কোণের আলোচনা দুই সরলকোণ পর্যন্ত সীমিত রাখা হয় এবং এরূপ জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক কোণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু যদি মনে করা হয় যে, OA রশ্মিটি সম্পুর্ণরূপে একবার ঘুরার পর আরও কিছু বেশি ঘুরে OA অবস্থানে গেল, তখন উৎপন্ন XOA কোণের পরিমাণ চার সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর। এরূপ ঘূর্ণনের ফলে ত্রিকোণমিতিতে আরও বৃহত্তর কোণ উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু সমতল জ্যামিতিতে চার সমকোণের চেয়ে বেশি ধারণা করা যায় না। OA রশ্মির আদি অবস্থান ∠XOX কোণকে জ্যামিতিতে কোণ বলে গণ্য করা হয় না, কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে ∠XOX কোণের পরিমাণ শূন্য ধরা হয়।
ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কোণ
উপরের আলোচনায় আমরা OA রশ্মিকে (উপরের চিত্রে) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়েছি এবং OA রশ্মি দ্বারা বিভিন্ন চতুর্ভাগে উৎপন্ন কোণসমূহকে ধনাত্মক কোণ হিসাবে বিবেচনা করেছি। সুতরাং কোনো রশ্মিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (anticlockwise) ঘুরালে উৎপন্ন কোণকে ধনাত্মক (positive) কোণ বলা হয় এবং কোনো রশ্মিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে (clockwise) ঘুরালে উৎপন্ন কোণকে ঋণাত্মক (negative) কোণ বলা হয় ।
তাই, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় একটি ধনাত্মক কোণের পরিমাপ 90° অপেক্ষা কম হলে ১ম চতুর্ভাগে থাকবে। আবার 360° ও 450° এর মধ্যে থাকলেও কোণটি ১ম চতুৰ্ভাগেই থাকবে। একইভাবে কোনো ধনাত্মক কোণের মান 180° ও 270° এর মধ্যে থাকলে কোণটি ৩য় চতুর্ভাগে, 90° থেকে 180° এর মধ্যে থাকলে ২য় চতুর্ভাগে এবং 270° ও 360° এর মধ্যে থাকলে ৪র্থ চতুর্ভাগে থাকে।
অনুরূপভাবে একটি ঋণাত্মক কোণের পরিমাপ – 90° থেকে 0° এর মধ্যে থাকলে ৪র্থ চতুৰ্ভাগে, – 180 থেকে 90° – এর মধ্যে ৩য় চতুর্ভাগে, – 270° থেকে – 180° এর মধ্যে ২য় চতুর্ভাগে ও – 360° থেকে – 270° এর মধ্যে হলে ১ম চতুর্ভাগে থাকবে। 180° ও 360° বা এর যেকোনো পূর্ণসাংখ্যিক গুণিতক XOX’ রেখার এবং 90° ও 270° বা এদের যেকোনো পূর্ণসাংখ্যিক বিজোড় গুণিতক YOY’ রেখার (উপরের চিত্রে) উপর অবস্থান করবে। ∠AOA 1 ১ম চতুর্ভাগে, ZAOA 2 ২য় চতুৰ্ভাগে, ZAOA 3 ৩য় চতুর্ভাগে এবং ZAOA4 ৪র্থ চতুর্ভাগে অবস্থান করে।
উদাহরণ ১.
ক) 430° ও খ) 545° কোণদ্বয়ের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে নির্ণয় কর।
ক) 430° = 360° +70° = 4 x 90° + 70° । 430° কোণটি ধনাত্মক কোণ এবং 4 সমকোণ = = অপেক্ষা বড় কিন্তু 5 সমকোণ অপেক্ষা ছোট। সুতরাং 430° কোণটি উৎপন্ন করার জন্য কোনো রশ্মিকে 4 সমকোণ বা একবার সম্পূর্ণ ঘুরার পর আরও 70° ঘুরতে হয়েছে (নিচের বামের চিত্র)। তাই 430° কোণটি ১ম চতুর্ভাগে অবস্থান করে।

খ) 545° = 540° + 5° = 6 x 90° + 5° । 545° কোণটি ধনাত্মক এবং 6 সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কিন্তু 7 সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। 545° কোণটি উৎপন্ন করতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে কোনো রশ্মিকে 6 সমকোণের চেয়ে 5° বেশি বা একবার সম্পূর্ণ ঘুরে আদি অবস্থানে আসার পর আরও দুই সমকোণের চেয়ে 5° বেশি ঘুরতে হয়েছে (উপরের ডানের চিত্র)। তাই 545° কোণটি তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করে।
উদাহরণ ২.
ক) – 520° ও খ) – 750° কোণদ্বয় কোন চতুর্ভাগে আছে নির্ণয় কর।

‘
ক) – 520° = – 450° – 70° = – 5 x 90° – 70° । – 520° একটি ঋণাত্মক কোণ এবং – 520° কোণটি উৎপন্ন করতে কোনো রশ্মিকেঘড়ির কাঁটার দিকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে একই দিকে আরো এক সমকোণ বা 90° এবং 70° ঘুরে তৃতীয় চতুর্ভাগে আসতে হয়েছে (উপরের বামের চিত্র)। সুতরাং, –540° কোণটি তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করছে।
খ) – 750 ° = -720° – 30° – = 8 x 90° – 30° । – 750° কোণটি ঋণাত্মক কোণ এবং ঘড়ির কাঁটার দিকে দুইবার সম্পূর্ণ (৪ সমকোণ) ঘুরার পর একই দিকে আরও 30° ঘুরতে হয়েছে (উপরের ডানের চিত্র)। সূতরাং – 750° কোণটির অবস্থান চতুর্থ চতুর্ভাগে।
